

গিগ ইকোনমি –গিগ ওয়ার্কার: পুঁজির শোষণ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে
সন্তোষ সেন
(বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ)
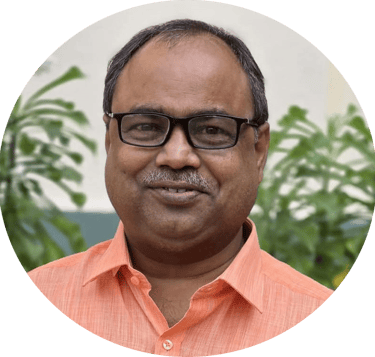
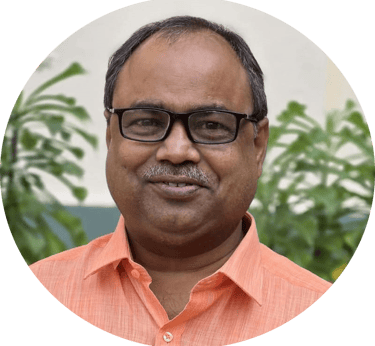
গিগ ইকোনমি হল ইন্টারনেট এবং অ্যাপের উপর নির্ভরশীল একটা মুক্ত এবং বিশ্বব্যাপী বাজার ব্যবস্থা, যেখানে কর্মসংস্থান সাময়িক এবং মজুরি নামমাত্র। প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্পমেয়াদী চুক্তির মাধ্যমে তাদের ইচ্ছামতো কর্মীদের দক্ষতা অনুযায়ী একটা ভদ্রস্থ মাইনের অনেক নিচে কাজে নিয়োগ করে এবং কর্মীদের কাজের পরিমান এবং উপভোক্তার দেওয়া মূল্যায়নের (রেটিংস) ওপর পারিশ্রমিক প্রদান করে। বলাই বাহুল্য যে, চাকরি শেষে কোম্পানির আর কোন দায় দায়িত্ব নেই। দিনে ১২-১৬ ঘণ্টা দৌড়ে আজকের "রানার" রা পিঠে ব্যাগ বা গাড়িতে আরোহী নিয়ে কাটিয়ে দিতে বাধ্য হয় জীবনের এক অমূল্য সময়। এইভাবেই গিগ প্ল্যাটফর্ম বদলে দিচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি এবং চাকরি বা ব্যবসার পরিবেশ।
এই অর্থনীতির জগতের নামকরণ গিগ হলো কেন? যেহেতু এই ক্ষেত্রে কাজ পুরোটাই চুক্তিভিত্তিক এবং অবশ্যই স্বল্প সময়ের জন্য, তাই একে 'গিগ ' বলা হয়। অর্থনৈতিক কোন প্রেক্ষাপটের ওপর দাঁড়িয়ে এই নিদারুণ ভবিতব্যের মুখোমুখি মানব সভ্যতা সেই ইতিহাস এবং এইসব কর্মীদের অসহনীয় জীবন- যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করব এই নিবন্ধে।
গিগ ও প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতির জমি তৈরি হল যে পথে:
প্রথমেই দেখা যাক শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব হল কিভাবে? পুঁজিবাদী যুগের শুরুতে ছোট - মাঝারি কারখানায় একই ক্যাটাগরির কাজে শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন ছিল প্রকটভাবেই। এই বিভাজনের বিরুদ্ধে একই কাজে সম-মাইনে এবং সমতার দাবিতে শ্রমিকরা আন্দোলন, অবরোধ, ধর্মঘট করতে শুরু করলেন এবং এ লড়াই কারখানায় চত্বর থেকে বেরিয়ে সমাজকাঠামোয় ছড়িয়ে পড়ল। অন্যদিকে শ্রমিকদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সহযোগিতা- সহমর্মিতা ও যুথবদ্ধতাকে ভাঙার জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়ে রাষ্ট্র ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্যদিকে নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় করার লড়াই আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই শ্রমিকরা 'শ্রেণী' হিসেবে সংগঠিত হলেন। শ্রমিকদের সমতার দাবির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা নিয়ে এল 'সাপ্লাই- ডিমান্ড' এর তত্ত্ব। এই তত্বের মূল নির্যাস – শ্রমিকদের সরবরাহ বেশি থাকলে স্বভাবতই চাহিদা কমবে এবং তাঁরা মজুরি কম পাবেন। পুঁজিবাদের এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে মার্কস কলম ধরলেন। ক্যাপিটালের প্রথম খন্ডে তিনি স্পষ্ট করে বললেন –" পুঁজি দুইদিকে একযোগে কাজ করছে। তার সঞ্চয়ন যদি একদিকে শ্রমের চাহিদা বাড়ায়, অপরদিকে সে শ্রমিকদের 'মুক্ত করে দিয়ে' শ্রমের সরবরাহ বাড়ায়; সঙ্গে সঙ্গে আবার বেকারদের চাপ কর্মে নিযুক্তদের বাধ্য করে আরও শ্রম যোগাতে; অতএব শ্রমের সরবরাহকে কিছু পরিমাণে শ্রমিকদের সরবরাহ থেকে স্বাধীন করে তোলে। এই ভিত্তিতে শ্রমের সরবরাহ ও চাহিদার নিয়মের ক্রিয়া পুঁজির স্বেচ্ছাচারিতাকে সম্পূর্ণ করে তোলে। কিন্তু যেই শ্রমিকরা গোপন রহস্যটা জেনে ফেলে – যে পরিমাণে তারা কাজ বেশি করে, যে পরিমাণে অন্যদের জন্য বেশি ধন উৎপাদন করে এবং যত তাদের শ্রমের উৎপাদন শক্তি বাড়ে, ঠিক সেই পরিমাণে কিভাবে পুঁজির আত্মপ্রসাদের উপকরণ হিসেবে তাদের ভূমিকা পর্যন্ত তাদের নিজেদের পক্ষে ক্রমশ আরও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়; যেই শ্রমিকরা আবিষ্কার করে যে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতার মাত্রা সম্পূর্ণতই নির্ভর করে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত- জনসংখ্যার চাপের উপর (অর্থাৎ কারখানার বাইরে প্রচুর শ্রমিক কাজ পাওয়ার দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে); যেই ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির সাহায্যে তারা কর্মরত ও বেকারদের সঙ্গে একটা নিয়মিত সহযোগ সংগঠিত করে তোলার চেষ্টা করে যাতে করে তাদের শ্রেণীর উপর পুঁজিবাদী কায়দার উৎপাদনের এই স্বাভাবিক নিয়মটির মারাত্মক ফলাফলকে দুর্বল বা নষ্ট করতে পারে; সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির স্তাবক, অর্থশাস্ত্রবিদরা চিৎকার করে ওঠে সরবরাহ ও চাহিদার ' শাশ্বত ' ও ' পবিত্র ' নিয়মকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে। কর্মরত ও বেকারদের যেকোন সংযোগ এই নিয়মের ' সুসমঞ্জস ' ক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অপরদিকে পুঁজি এই অসুবিধাজনক ক্রিয়াকে পীড়নমূলক উপায়ে ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিহত করার চেষ্টা করে"। [কার্ল মার্কস: পুঁজি, প্রথম খন্ড (দ্বিতীয় অংশ), প্রগতি প্রকাশন, পৃষ্ঠা: ১৭০-১৭১]
মার্কসের এই সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাই মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বে। শ্রমিকদের সমমজুরি এবং সমতার দাবির সাথে যুক্ত হলো বুর্জোয়াদের "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্লোগান। শ্রমিক শ্রেণী এই দাবিকে সামনে রেখে বুর্জোয়াদের সাথে একযোগে ফ্রান্সের সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সম্রাট পরাজিত হওয়ার পর দ্বিতীয় নেপোলিয়নকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা হল মালিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে। এর পরপরই শ্রমিকদের সব দাবিদাওয়া নস্যাৎ করে তাঁদের
সংগঠিত শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করতে ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে শ্রমিকদের আন্দোলনের ওপর গুলি চলে। শ্রমিকরা জীবন দিয়ে বুঝলেন – পুঁজির এই শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিকদেরও পাকাপোক্ত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। তাঁরা বুর্জোয়াদের সঙ্গ ত্যাগ করে প্রকৃত অর্থে শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত হলেন এবং এই অভিজ্ঞতার ধাাবাহিকতায় ১৮৭১ সালে গড়ে উঠল 'প্যারি কমিউন'। পৃথিবীর মানুষ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন – শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত একটি উন্নত সমাজের রূপরেখা কেমন হতে পারে। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণি প্রমাদ গুনল। ফ্রান্স সহ ইউরোপের বুর্জোয়ারা তাদের সমস্ত শক্তি সংগঠিত করে প্যারিকে চারদিক দিয়ে ঘিরে
একটি উন্নত নতুন সমাজের অঙ্কুর ৭১ দিনের শিশু 'প্যারি কমিউন'কে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। শুধুমাত্র প্যারি শহরের শ্রমিকরা এই অসম লড়াইয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলেন। তাঁরা বুঝলেন যে, এখন আর এভাবে এগোন যাবে না। তাই বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যেই আটঘন্টার কাজের দাবির (আটঘণ্টা শ্রমশক্তি বিক্রি, আটঘণ্টা বিশ্রাম এবং বাকি সময়টুকু তাঁদের বিনোদন ও পরিবারের সাথে সময় কাটানো) এবং সম - মজুরি ও সমতার লড়াইকে তাঁরা তীব্র করলেন। ১৮৮৬ সালে এসে শ্রমিকদের এই লড়াই বিশ্বজনীন চেহারা নিল, শ্রমিকশ্রেণী আন্তর্জাতিক হলেন। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের চাপে মালিকপক্ষ আটঘণ্টা কাজের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হল।
এরপর ১৯১৭ তে রাশিয়ার সফল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র ' প্রতিষ্ঠিত হলে বুর্জোয়া শ্রেণীর মাথা আবারো ঘুরে গেল। শ্রমিকশ্রেণীর এই আগুয়ান ও সংগঠিত শক্তিকে সামলাতে ১৯২০ সালে মালিকপক্ষ সামনে আনল 'নিউ লিবারেল অর্থনীতির ' তত্ত্ব। সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর যুথবদ্ধতাকে ভাঙতে এই তত্ত্ব নিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী দাপিয়ে ব্যাট করে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। বলাবাহুল্য যে, আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্ব পুঁজিবাদ রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে একদিকে অবরোধের অর্থনীতি (Sanction economy) এবং অত্যন্ত সুচতুরভাবে 'শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র ' র বিরুদ্ধে ব্যক্তির তথাকথিত স্বাধীনতা ও ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রচার - প্রপাগান্ডা চালিয়ে গেল। এই আলোচনা অন্যত্র অন্য সময়। ফিরে আসি পুঁজির আন্তর্জাতিক চরিত্র নিয়ে।
কেইন্স ' র তত্ত্বকে সামনে রেখে ১৯৪৪ সালে 'ব্রেটন উডস ' সম্মেলনের মধ্য দিয়ে পুঁজির আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো গঠন করা হল। কিন্তু ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস! ১৯৪৩ সালেই 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' ভেঙে দিয়ে কমিউনিস্টরা জাতীয় স্তরে, এমনকি একটি কারখানার ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় পুঁজির আন্তর্জাতিক শক্তিকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হলেন। এতকাল ধরে চলে আসা এক ব্যবস্থা – যে কোন মুদ্রার সাথে সোনার (gold) তুল্যমূল্য বিচারের মাপকাঠি থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৭৩ সালে আমেরিকার ডলারকে তেল-অর্থনীতির সাথে যুক্ত করা হল। এর আগেই ১৯৭১ সালে 'ব্রেটন - উডস ' কাঠামো ভেঙে দেওয়া হয়। ক্রুড পেট্রোলিয়াম কেনাবেচা শুধুমাত্র ডলারের মধ্য দিয়েই করতে হবে – এই ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ডলার সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার লাভ করল। নব্বইয়ের দশকে এসে নয়া উদার অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে বড় বড় কারখানা ও সংস্থাগুলোকে ভেঙ্গে টুকরো করা হল। 'ভার্টিক্যাল ডিভিশন অফ লেবার ' র মধ্য দিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উপকরণকে তৃতীয় বিশ্বের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে দেওয়া হল। সস্তা শ্রম ও অগাধ প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করে পুঁজির 'ভেলোসিটি অফ টার্নওভার ' অনেক বেড়ে গেল ঠিকই। সাথে সাথে বিশ্বজুড়ে দুটো লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটে গেল।
এক: শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত শক্তি ও যুথবদ্ধতাকে ভেঙে তাঁদের একক ব্যক্তিমানুষে পরিনত করা হল, ফলে মালিকশ্রেণীর নয়া নয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁরা সংগঠিতভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে সেভাবে রুখে দাঁড়াতে পারলেন না।
দুই: সারা বিশ্বে কার্বন নিঃসরণ বেড়ে গেল প্রচুর পরিমাণে (২০২০ সালে এসে যা ৪০ বিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছে গেছে), পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। সমুদ্র জলের তাপমাত্রা ও জলস্তর বেড়ে গেছে বহুল পরিমাণে, হিমালয় ও মেরু প্রদেশের বরফের চাদর গলছে অতি দ্রুত হারে। কর্পোরেটের স্বার্থে কৃষিকাজে রাসায়নিক সার ও বিষ প্রয়োগের ফলে জলের দূষণ ও সংকট বেড়েছে বহুগুণ, জল ও খাদ্য শৃঙ্খলে বিষ ঢুকে পড়ায় মানুষের রোগ অসুখ দিন দিন বাড়ছে, বায়ুদূষণের কবলে শ্বাসকষ্ট সহ ফুসফুসের নানান রোগ এমনকি কালান্তক ক্যান্সারও আজ ঘরে ঘরে। এককথায় রাসায়নিক চাষের ফলে কৃষিবাস্তুতন্ত্র এক সামগ্রিক সংকটে, কৃষকরা বিপন্ন হচ্ছেন বারবার (প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই বিপন্নতাকে আরো বাড়িয়েছে)। জলবায়ুর পরিবর্তন আজ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুঁজির অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একদিকে বিপর্যস্ত হচ্ছে প্রকৃতি পরিবেশ ও মানুষ সহ তামাম প্রাণী জগৎ। পাশাপাশি মানুষ হয়েছে সমাজ ও প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজ (এর মধ্যে টিকে থাকা কয়েকটি সংগঠিত শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের শ্রমিক এবং উচ্চ মাইনের সরকারি কর্মীরাও আছেন) শুধুমাত্র টাকা উপার্জন ও ভোগ্যপণ্যের বাজারের পিছনে অন্ধভাবে ছুটতে গিয়ে এক স্বার্থপর ব্যক্তি মানুষে পরিণত হয়েছে (সমাজ বিচ্ছিন্ন এইসব একাকী মানুষের মানসিক অবসাদ, হতাশা বেড়েছে বহুগুণে)। চামড়ার মধ্যে আবদ্ধ তাদের রক্ত মাংসের ছোট শরীরটাকেই বৃহৎ হিসেবে ভাবছে, এর বাইরে যে তার সত্যিকারের বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ 'এক্সটেন্ডেড বডি ' – যেমন পাহাড়, নদী, আকাশ, সমুদ্র তাকে তুচ্ছ করে ডাস্টবিনে পরিণত করেছে। ফলে গ্রাম থেকে শহরে, স্থলের সাথে সমুদ্রের মধ্যে বিপাকীয় ফাটল (মেটাবলিক রিফ্ট) বেড়েছে। বেড়েছে মানুষের সাথে প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতা। তাই এই বিপর্যস্ত ও বদলে যাওয়া প্রকৃতি পরিবেশ মেরামতির দাবিতে বিশ্বজুড়ে কচিকাঁচারা আন্তর্জাতিক আন্দোলনের রূপরেখা হাজির করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা বড়রা, প্রাজ্ঞরা এর সাথে যুক্ত হতে পারছি না।
পুঁজির সারপ্লাস ভ্যালু শ্রমিকদের কোথায় ঠেলে দিল:
পুঁজির সঞ্চয়ন ও মুনাফা বৃদ্ধির হারকে বজায় রাখতে সারপ্লাস ভ্যালু বা উদ্বৃত্ত মূল্যকে ক্রমাগত বাড়িয়েই চলতে হয়। তাই শ্রমিকদের টুকরো করার পর এবার পুঁজির নজর পড়ল তাদের পরিবারের ওপর। হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর বাড়ি ফিরে শ্রমশক্তির পুনরুদ্ধার (যাতে পরের দিন শ্রমিক আবার শ্রমশক্তি বেচতে পারে) করার জন্য স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের শ্রমের (রান্নাবান্না সহ গৃহস্থালির নানান কাজে) ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হতেন। সহযোগিতা - সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এই পারিবারিক যূথবদ্ধতাকেও গ্রাস করে পুঁজির লম্বা হাত, পরিবারের সদস্যদের শ্রমকেও টেনে আনল পুঁজির উৎপাদনের জগতে। এর মধ্য দিয়ে একই মজুরি দিয়েও পুঁজির উদ্বৃত্তমূল্য দ্বিগুণ হয়ে গেল। শ্রমিক সরবরাহ বাড়িয়ে কম মজুরি দিয়ে স্বামী- স্ত্রী বা পরিবারের অন্য সদস্যদের শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করার জন্য জন্ম দেওয়া হল প্ল্যাটফর্ম প্রযুক্তির। কোন কারখানা স্থাপন বা সেই অর্থে মানুষের ব্যবহারযোগ্য কোন পন্য উৎপাদন না করে এবং বিরাট অংকের পুঁজি বিনিয়োগ না করেও প্রযুক্তির সাহায্যে মূলত অ্যাপনির্ভর মার্কেটিং ও সার্ভিস সেক্টরে বিপুল বেকার বাহিনীকে কাজে লাগানো হল অত্যন্ত কম মজুরিতে চুক্তিভিত্তিক স্বল্পকালীন অস্থায়ী কর্মী হিসেবে। জন্ম নিল গিগ ইকোনমি ও গিগওয়ার্কার শব্দগুলো। যার হাত ধরে কর্মীদের জীবন যন্ত্রণা বেড়ে গেল বহুগুনে। পুঁজির বিকাশের যুগে স্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিক এবং কায়িক ও মানসিক শ্রমের বিভাজন তো ছিলই। উদার অর্থনীতির যুগে কল-কারখানা, শিল্পসংস্থা নানান জায়গায় ছোট ছোট আকারে ছড়িয়ে পড়ায় উদ্ভব হল পরিযায়ী শ্রমিকদের। তবুও এই অংশের একটা শ্রমিক পরিচয় (আইডেন্টিটি অফ লেবার) ছিল কোন-না-কোন উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাকার কারণে। কিন্তু গিগ ওয়ার্কাররা উৎপাদনের জগতে সরাসরি যুক্ত না থাকায় শ্রমিক পরিচয় ঘুচিয়ে কেবলমাত্র কর্মীবাহিনী হিসেবে চিহ্নিত হল। শ্রমিক নয় বলেই তাদের জন্য শ্রমকোডের কোন বালাই নেই; নেই সংগঠন করার অধিকার। কাজের নিশ্চয়তা ও চাকরি শেষে আর্থিক নিরাপত্তা – এইসব প্রশ্ন তোলা মানা। বরং প্রযুক্তির সাহায্যে সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে এইসব কর্মীদের কাজের ওপর নজরদারি বাড়ানো হল। ঠিক সময়ে গরমাগরম খাবার খদ্দেরদের কাছে পৌঁছেছে কিনা, সঠিক সময়ে যাত্রীকে গাড়িতে তোলা - নামানো হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি, সব অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল বা কম্পিউটারের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগল।
আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যা:
এই ইকোনমির বাস্তব ভিত্তি মার্কসের চোখে ধরা পড়েছিল ১৮৪০- ৫০ সময়কালেই। ক্যাপিটালের প্রথম খন্ডে 'আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার বিভিন্ন রূপ ' শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়টিকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। তাঁর কথাতেই ফিরি আমরা – "কারখানাগুলোতে সমস্ত বড় বড় কর্মশালার মতোই, যেখানে যন্ত্রপাতি একটি নির্ধারকরূপে প্রবেশ করেছে, অথবা যেখানে শুধু আধুনিক শ্রমবিভাজন কার্যকর হয়েছে, সেখানে বিরাট সংখ্যায় বালক (শিশু, কিশোর- কিশোরী) কাজে নিযুক্ত হয়। পরিণত বয়সে তাদের খুব অল্পসংখ্যকই শিল্পের সেই একই শাখায় কাজ পায়, বরং অধিকতর সংখ্যায় নিয়মিত কর্মচ্যুত হয়। এই অধিক সংখ্যক ভাসমান উদ্বৃত্ত-জনসংখ্যার একটা অংশ দেশ থেকে বাইরে চলে যায় (পরিযায়ী শ্রমিক), প্রকৃতপক্ষে বহির্গত পুঁজিকে অনুসরণ করেই যায়। এর ফলে পুরুষের তুলনায় নারী কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়"। এর পরেই মার্কস পুঁজির নিজস্ব দ্বন্দ্বের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিককে সামনে আনছেন – "শ্রমিকসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি পুঁজির সঞ্চয়নের প্রয়োজনকে মেটাতে পারেনা, অথচ এ সংখ্যা সবসময় সেই প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত, এটাই হলো পুঁজির গতিবিধির সহজাত দ্বন্দ্ব। পুঁজি চায় অধিকতর সংখ্যায় যুবক শ্রমিক, স্বল্পতর বয়স্ক শ্রমিক। পুঁজির দ্বারা শ্রমশক্তির ব্যবহার এত দ্রুত যে, জীবনের অর্ধেক পার হলেই শ্রমিক প্রায় তার গোটা জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলে। ফলে সে ওই অতিরিক্তদের দলে পড়ে যায়" (পৃষ্ঠা - ১৭২, ঐ)। অর্থাৎ এককথায় – সবসময় একটা বাড়তি বেকার বাহিনী বা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে সস্তায় শ্রমশক্তি কিনে পুঁজি তার সঞ্চয়নকে নিত্য বাড়িয়ে তোলে।
তথ্য ও পরিসংখ্যান কী বলছে:
সংসদের বাদল অধিবেশনে (২০২২) এক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে পেশ করা সরকারি তথ্য বলছে -- বিগত আট বছরে মোদি জামানায় মাত্র ৭,২২০০০ মানুষ স্থায়ী সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত হয়েছেন, যদিও এই সময়ে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ২২ কোটি ৫ লক্ষ। অর্থাৎ এই বিপুল বেকার বাহিনীর মধ্যে বছরে আট লক্ষ মানুষেরও চাকরি হয়নি। চাকরি হবে কোথায়? সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত বৃহৎ সব সংস্থাগুলোকে তো শুকিয়ে মারা হয়েছে বা সস্তায় কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঠিকা, পরিযায়ী শ্রমিক ও গিগ - কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। BLS (Bureau Of Labor Statistics Of The United States Department Of Labor) ' র তথ্য অনুসারে ২০১৭ সালে গিগ অর্থনীতিতে আমেরিকার সাড়ে পাঁচ কোটি কর্মী যুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ আমেরিকার মোট শ্রমিক কর্মচারীর ৩৬ শতাংশই যুক্ত আছেন এই তথাকথিত স্বাধীনভাবে নিজের সুবিধামতো সময়ে কাজ করার গিগ প্লাটফর্মে এবং ৩৩ % কোম্পানির বেশিরভাগ কর্মীই হলেন গিগার। আমেরিকার মতো দেশেও বেকারত্বের হার উর্দ্ধগামি হওয়ায় নতুন করে আরো প্রচুর মানুষ গিগ প্লাটফর্মে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কাজ খুঁজে নিতে বাধ্য হবেন। এটা ঠিক যে একাংশের কর্মী / শ্রমিক স্থায়ী চাকরির পাশাপাশি কিছু বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে এই প্লাটফর্মে কাজ করেন। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো – আমেরিকার মোট গিগারদের ৪৪ শতাংশেরই প্রধান আয়ের উৎস হলো গিগ ইকোনমির জগতে এবং ১৮ - ৩৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ৫৩ শতাংশই যুক্ত চুক্তিভিত্তিক সার্ভিস ও মার্কেটিং সেক্টরের পরিসরে।
ভারতের অর্থনীতিতেও গিগ শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে হুহু করে। 'বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ' আর 'মাইকেল অ্যান্ড সুজান ডেল ফাউন্ডেশন' একটি গবেষণায় জানিয়েছে – আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যে ভারতের গিগ অর্থনীতি প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে যেখানে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান এই গিগ অর্থনীতিতে হচ্ছে তা বেড়ে হবে ২.৪০ কোটি। আর আগামী আট থেকে দশ বছরের মধ্যেই প্রায় নয় কোটি মানুষ এই অর্থনীতির মধ্যেই কর্মসংস্থান পাবেন, কারণ মূলধারার অর্থনীতি আরও সঙ্কুচিত হবে ও সুরক্ষিত কর্মসংস্থান অতীতের বস্তুতে পরিণত হবে। TGI (Taskmo Gig Index)' এর তথ্য বলছে– আমাদের দেশে সক্রিয় গিগ কর্মীর সংখ্যা এই বছরে প্রথম পাঁচ মাসে ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ কিছু সংস্থায় গিগকর্মীর বৃদ্ধি হয়েছে ২০০ থেকে ৩০০ শতাংশ। এই সময় জুড়ে হায়দারাবাদ, মুম্বাই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু আর চেন্নাই এর মতো শহরে গিগ কর্মীর সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রেও ৪৮% গিগ কর্মী হল ১৯-২৫ বছর বয়সী নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা, যাদের কাছে স্থায়ী চাকরির সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। আর এই ক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যা ২৮ শতাংশের আশেপাশে, তাঁরা চাইছেন পড়াশোনা বা সংসারের কাজ সামলে নিজেদের সুবিধামতো ফ্লেক্সিবেল কাজে যুক্ত হয়ে পড়াশুনার খরচ তুলতে বা এই দুর্মূল্যের বাজারে সংসারের জন্য কিছুটা বাড়তি উপার্জন করার তাগিদে।
সরকারি দপ্তরও এই তথ্য স্বীকার করেছে। নীতি আয়োগ অতি সম্প্রতি একটি রিপোর্ট (India's booming Gig and Platform Economy) প্রকাশ করেছে। যার মূল নির্যাস –আগামী আট বছরের মধ্যে আমাদের দেশে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী এবং প্ল্যাটফর্ম কর্মীর সংখ্যা ২ কোটি ৩৫ লক্ষে গিয়ে দাঁড়াবে অথচ ২০২০-২১ অর্থবর্ষে এই সংখ্যাটা ছিল মাত্র ৭৭ লক্ষ। এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, আগামী দিনে ভারতসহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই স্থায়ী চাকরি, মাস গেলে মোটামুটি একটা ভদ্রস্থ মাইনে, ডি এ, অবসরকালীন গ্র্যাচুইটি, পেনশন এইসব জাদুঘরে জায়গা নেবে। যে ভবিষ্যৎ পড়ে থাকবে তা হলো দুবেলা-দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকতে হলে ৩৬৫ দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা - রাত্রি দৌড়াতে হবে স্বল্পমেয়াদী চুক্তির অস্থায়ী চাকরির পিছু পিছু। শরীর স্বাস্থ্য ও খাওয়া - দাওয়ার তোয়াক্কা না করে জীবন হাতে নিয়ে শুধু দৌড় দৌড় আর দৌড়, না হলে জীবনের স্পন্দন যাবে থেমে। মানবসম্পদের কি চূড়ান্ত অবমাননা করে চলেছে বর্তমান যুগের এই গিগ অর্থনীতি।
গিগ ওয়ার্কারদের কাজের ক্ষেত্র এবং কাজের শর্ত:
গিগ অর্থনীতির জগতে মূলত ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর সার্ভিস সেক্টরে ও মার্কেটিংয়ে মানুষ কাজ পাবেন মাসিক ১০-১২ হাজার টাকার মজুরিতে, থাকবে না কোন পেনশন গ্র্যাচুইটি, চাকরি শেষে মালিককে কোন দায় দায়িত্ব নিতে হবে না। আর এই গিগ প্ল্যাটফর্মের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মাইনে নির্ভর করে কাজের দিন ও ঘণ্টার পরিমাণের ওপর। কোন সাপ্তাহিক ছুটির বালাই নেই। কাজে না এলে মাইনেও নেই। অর্থাৎ সংকুচিত কর্মসংস্থানের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খুদ কুঁড়ো ছিটিয়ে সস্তার শ্রমিক বাহিনী তৈরির এক বৃহৎ পরিসর এই গিগ প্ল্যাটফর্ম। মায় বিভিন্ন কারখানাতেও এই প্রথায় নিয়োগ শুরু হয়েছে। আর সরকারি ক্ষেত্রে নতুন করে চুক্তিতে ঠিকা কর্মী নিয়োগের নমুনা তো আমরা লক্ষ্য করলাম অগ্নিপথ প্রকল্পে, সরকারি সব দায় দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে অগুণিত বেকার বাহিনীর অমূল্য মানবসম্পদকে জলের দরে কিনে নিয়ে "দেশপ্রেমিক" তৈরির সুকৌশলী প্রচেষ্টা। এই পথ ধরে ব্যাংকেও শুরু হতে চলেছে গিগ চুক্তির ভিত্তিতে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ। আপাতত যেটুকু জানা যাচ্ছে তা হলো – স্টেট ব্যাংক, ব্যাংক অফ বরোদা সহ বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সাধারণ এবং উচ্চপদস্থ কিছু অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে চুক্তির ভিত্তিতে। ব্যাংক ইউনিয়নগুলো খুব সঙ্গত ভাবেই অভিযোগ করেছেন যে, ব্যাংকশিল্পে কর্মী ও আধিকারিকদের সংগঠনকে দুর্বল করে দেবার উদ্দ্যেশে এই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের উদ্যোগ। সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন –" ব্যাংক শিল্পে কর্মী ও অফিসার মিলে ৪১ হাজার পদ খালি আছে, এছাড়া নিয়মিত ভাবে অবসর নিচ্ছেন বহু কর্মী"।
গিগ ওয়ার্কারদের কাজের জায়গাগুলো হলো – ওলা উবের এর মতো ট্যাক্সি ড্রাইভার, সুইগি জোম্যাটো এর মতো নানান দোকান থেকে নানান কিসিমের খাবার সংগ্রহ করে উপভোক্তার বাড়িতে সরবরাহ করার কাজে ডেলিভারি বয় বা গার্ল ; অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, জিও-মার্ট এর মতো অনলাইন শপিংয়ের দুনিয়ায় বাইকে করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্ডার করা মাল সরবরাহ করা। অধুনা এর সাথে যুক্ত হয়েছে শহরাঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন কোম্পানির (Rapido, Ola, Uber..) অ্যাপ ব্যবহার করে স্কুটি বা বাইকে আরোহীকে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজে যুক্ত এক বিপুল যুবা বাহিনী।
আলোচিত ক্ষেত্রগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল –কোম্পানিগুলো ব্যবসা করছে প্রায় কিছু মূলধন বিনিয়োগ না করেই, তারা কিন্তু পুরোপুরি উৎপাদন জগতের বাইরে। এমনকি 'গিগ ড্রাইভারদের ' চারচাকা বা দুইচাকার গাড়ি দেওয়ার বাধ্যবাধকতাও নেই। অফিসের স্থান এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য বিনিয়োগও প্রায় শূন্যের ঘরে। শুধুমাত্র বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতির সাহায্যে সরকারি ব্যস্থাপনায় ও জনগণের করের টাকায় চালু থাকা ইন্টারনেট ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের নামে একটি নির্দিষ্ট অ্যাপ তৈরি করে নিলেই হল। তারপর সেই অ্যাপে কর্মপ্রার্থীদের যুক্ত করে নাও, আর খদ্দের ধরার জন্য তাঁদের ব্যবহৃত সোশ্যাল মিডিয়ায় এই পরিষেবার বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দাও আর নেটওয়ার্কের দুনিয়ার এইভাবে উপভোক্তাদের যুক্ত করে নাও এবং এইসবই প্রায় মুফতে।
সমাজের বিশাল বেকার বাহিনীর এক অংশ অভাবের সংসারে দুমুঠো ভাত তুলে দেওয়ার জন্য ধারকর্জ করে বা জমিজমা বিক্রি করে নিজের গাড়ি নিয়ে হাজির অদৃশ্য কোম্পানির দুয়ারে সেই অ্যাপের সুতো ধরে। তারপর তো শুরু হলো জীবন হাতে নিয়ে দৌড় আর দৌড়, জোরে দৌড়াতে পারলে দুই পয়সা বেশি কমিশনের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে। আর প্যাসেঞ্জার তুলতে দেরি হলে বা খদ্দেরের বাড়িতে সময়মতো গরমাগরম খাবার পৌঁছে দিয়ে তাঁদের রসনার তৃপ্তি করতে না পারলে রেটিং যাবে কমে, কর্মীর কমিশন এমনকি চাকরি নিয়েও টানাটানি পড়বে। তাই উচ্চ মাইনের মধ্যবিত্ত সমাজের স্মার্ট বাবুবিবিগন যখন সপ্তাহান্তে বা সরকারি সবেতন ছুটির দিনে বাড়িতে বসেই স্মার্ট ফোনে আঙ্গুল স্পর্শ করে বিরিয়ানী এবং চিকেন কাবাব পৌঁছে দেওয়ার হুকুম সেরে খাবারের প্রত্যাশায় সময় নষ্ট করতে না পেরে ডেলিভারি বয়ের তুরন্ত্ ডেলিভারি করে দেওয়া খাবার গিলে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে তুলতে সুখের দিবানিদ্রার স্বপ্ন দেখেন, ঠিক তখনই আজকের যুগের 'গিগ রানারদের ' বাইকের স্পিড বাড়িয়ে পড়িমরি করে ছুটতে হয় অন্য কোন খাবার প্রত্যাশীর বাড়ির দরজায় কলিং বেল বাজাতে। কারণ, খারাপ ফিডব্যাকের ভূত সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়ায় তাদের। ওদের ছুটি নেই। বাইকের জ্বালানি খরচের ভারও বহন করতে হয় তাদের। কোম্পানি তো কানাকড়িও দেবে না, তাদের কাজ প্রায় কোন বিনিয়োগ না করেই বাড়ি বসে পায়ে পা তুলে অ্যাপের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে নাফার খতিয়ান মেলাতে ব্যস্ত থাকা। অন্যদিকে ফুড ডেলিভারির অনেক কোম্পানিতে কিছু গিগার আছে, যাদের কোম্পানির খাতায় রেজিস্ট্রেশন নেই, তাদের মাইনে কমেরও কম। একটি অর্ডার ডেলিভারি করে পাবে ২০ টাকা, মানে সারাদিন রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে মেরেকেটে দিনান্তে ৫০০ টাকা। তাদের অনেকের বাইক কেনার সামর্থ্য নেই। আর এই মাগ্গিগণ্ডার বাজারে অগ্নিমূল্য পেট্রোল কিনতে হলে বাস্তবত না খেয়ে থাকতে হবে। তাই বেশ কিছু ডেলিভারি বয় সাইকেল চেপে দিনরাত এক করে দৌড়চ্ছে আরো কয়েকটা বেশি অর্ডার নিয়ে খদ্দেরের ঠিকানায় সময়মতো হাজির হওয়ার উদগ্র বাসনায়। ফলে ঘটছে অনেক মর্মান্তিক ঘটনাও। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত (the print.in, 29.07.22) একটি খবরের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইব। ১৯ বছরের এক তরুণ তরতাজা যুবক সারাদিন সাইকেল উজিয়ে গাজিয়াবাদের তীব্র খরতাপ মাথায় নিয়ে জ্যোমাটোর কাস্টমারের দোরেদোরে তাদের পচ্ছন্দমতো সুস্বাদু খাদ্য পৌঁছে দিয়ে নিজে রাতের খাবার না খেয়ে বিছানায় নেতিয়ে পড়ে। তীব্র রৌদ্রে সারাদিন সাইকেল নিয়ে দৌড়ানোর ফলে তার খিদে নষ্ট হয়ে যায় আর সারা শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। যে খাবার ব্যাগে ভরে নিয়ে দৌড়য়, তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না ঠিকমতো না খেয়ে থাকা এই মানুষগুলো। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে গেলেও তারা অর্ডার সাপ্লাই রিফিউজ করার সাহস দেখায় না। সময়ে মাল পৌঁছে দিতে না পারলে হবে পেনাল্টি। কোম্পানির মুনাফা সচল রাখার নির্মম নিষ্ঠুর গতির কাছে কত অসহায় এই বেকার বাহিনীর দল। বাংলার একজন ডেলিভারি বয় কাজ থেকে ছাঁটাই হওয়ায় অবসাদে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। গিগ প্ল্যাটফর্মের কর্মীদের হতাশা অবসাদ মানসিক ক্লান্তি দিন দিন বাড়ছে। আগে জ্যোমাটো কোম্পানিতে আট ঘণ্টায় নয়টি অর্ডার ডেলিভারি করলে ডেলিভারি কর্মী ৫০০ টাকা কমিশন পেত। সেই কমিশন প্রথা তুলে দিয়ে আরো মুনাফা করার জন্য সংস্থাটি সময়ে স্লট বুকিং করতে পারলে ডেলিভারি পিছু কিছু টাকা ধরিয়ে দিচ্ছে। তাই কমিশন ফিরিয়ে আনা ও চালকদের বৈদ্যুতিক গাড়ি কোম্পানির তরফ থেকে সরবরাহ করার দাবিতে বিশ্বের নানান প্রান্তে ক্ষোভ বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটতেও দেখা যাচ্ছে। কাজের শর্ত উন্নত করা ও মাইনে বাড়ানোর দাবিতে ইউরোপের উবের চালকদের যূথবদ্ধ হয়ে অ্যাপ বন্ধ করে একযোগে রাইড রিফিউজ করার খবর হইচই ফেলে দেওয়ার পর ইউরোপিয়ান কমিশন গিগারদের সেল্ফ- এমপ্লয়মেন্ট স্টেটাস তুলে কোম্পানির কর্মী হিসাবে বিবেচনা করার একটি খসড়া তৈরি করতে বাধ্য হয়েছে।
কলকাতায় অ্যাপ-ভিত্তিক বাইক পরিষেবার কয়েকজন চালকের সাথে কথা বলে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা সংক্ষেপে এই রকম – যাত্রীদের থেকে প্রাপ্ত টাকার ১৫ % কেটে নেয় সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থা। এখানেই আসল মজা। কোনরকম বিনিয়োগ না করেই কোম্পানি প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীর থেকে এইভাবে কয়েক লক্ষ টাকা নাফা ঘরে তুলে নিচ্ছে। আবার এর মধ্যে চুরিও আছে। অনেক সময়ই কোন কারণ না দেখিয়ে ২৫-৩০ শতাংশ পর্যন্ত টাকা কেটে নেয় এইসব সংস্থাগুলো। এই পুকুর চুরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস পায় না গিগ ওয়ার্কাররা চাকরি নট হয়ে যাবার ভয়ে। আর সমস্ত ধরনের সার্ভিসের কাজে যুক্ত চালকদের গাড়ি পার্কিং নিয়ে পুলিশের সাথে ঝামেলা নিত্যদিন লেগে থাকে এবং গাড়ির কোন ডেমেজ হলে বা দুর্ঘটনা ঘটলে চুক্তিতে তার দায়ভার নেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবত এইক্ষেত্রে কোম্পানি সব দায়ভার নির্দ্বিধায় ঝেড়ে ফেলে। সার্ভিস প্রদানকারী কর্মীদের রেনকোট, পোশাক এমনকি ব্যাগ পর্যন্ত দেয় না কোম্পানি, সবটাই যায় গিগারদের পকেট থেকে। তবুও অন্তত দশ - বারো হাজার 'বাইক সার্ভিস' চলে কলকাতার রাজপথে। তথ্য বলছে সারা দেশজুড়ে শুধুমাত্র জ্যোমাটোর তিন লাখের বেশি 'সার্ভিস পার্টনার ' আছে। বেকারত্বের কী নির্মম জ্বালা! এই প্রসঙ্গে কলকাতায় ব্লিংকিট কোম্পানিতে শ্রমিকদের যৌথবদ্ব জেদী লড়াই ও তাদের প্রায় সব দাবিদাওয়া মানতে কোম্পানিকে বাধ্য করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করব।
২০২২ এর ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতার সমস্ত ব্লিংকিট হাবের ডেলিভারি শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। এই আন্দোলনে ওয়ার্কারদের প্রধান দাবি ছিল, ৫০ টাকা বেস পে চালু রাখতে হবে। আন্দোলনের চাপে পড়ে
৩০শে সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফার মিটিংয়ে গুরগাঁওয়ের কর্পোরেট অফিস থেকে কোম্পানির "পিপল অপারেশন" এর ডিরেক্টর সরাসরি মিটিং করতে আসেন। ওয়ার্কারদের ৫ জন প্রতিনিধির সাথে দীর্ঘক্ষণ মিটিং করার পর কোম্পানির তরফ থেকে নতুন ইন্সেন্টিভ স্ল্যাবের প্রস্তাব দেওয়া হয়। বলা হয় –৪০ টাকা অব্দি তারা দিতে পারবে। ওয়ার্কারা এই প্রস্তাব মেনে নিয়েই জানায় যে বেস পে তোলা চলবে না। দীর্ঘ দরকষাকষির পর মীমাংসা সূত্র না বেরোনোয় অধিকাংশ হাবের ওয়ার্কার স্ট্রাইক চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে মিটিং থেকে ফিরে যান। কোম্পানি চাপে পড়ে ১লা অক্টোবর রাতে সংশোধিত স্ল্যাবের প্রস্তাব দেয়, যেখানে আরো তিনটে স্ল্যাব যোগ করা হয়। এই সংশোধিত স্ল্যাব তুলনামূলকভাবে ব্লিংকিট ওয়ার্কারদের লড়াইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। অন্তত ৪০ টাকা বেস পে-র প্রধান দাবি অর্জন না হলেও, আপসহীন এই লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতে কোম্পানি অর্ডার প্রতি ২৫ টাকা বেস পে এবং সাথে কিছু টার্গেট পূরণ করলে ৪০ থেকে ৪৬ টাকা অব্দি পাওয়ার সুযোগ করে দিতে বাধ্য হয়। এরই সাথে বিশেষ কারণ দেখালে সপ্তাহে একদিন ছুটি, শনি-রবিবার ১০ ঘন্টার বদলে ৯ ঘন্টা কাজ ইত্যাদি নানা অধিকারও শ্রমিকরা অর্জন করেন। কিন্তু মালিক বোঝে মুনাফা, যেখানে মানবিকতা বা শ্রমিক স্বার্থ দেখার দায় গৌণ। আর তাই স্ট্রাইক প্রত্যাহার করে শ্রমিকরা কাজে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলে আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্বদায়ী 'কাঁটাপুকুর হাব' খোলার ব্যাপারে কোম্পানি গড়িমসি করতে থাকে। ওয়ার্কাররা ৭ দিন ধরে কাজে আসলেও, কোম্পানি এই হাব বন্ধ করে রাখে এবং অবশেষে জানিয়ে দেয় – এই হাব তারা আর খুলবে না। যারা এর পরেও ব্লিংকিটে কাজ করতে চায় তারা মুচলেকা দিয়ে নিকটবর্তী হাবে কাজে যোগ দিতে পারে। যে অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে ব্লিংকিটের ডেলিভারি শ্রমিকরা একজোট হয়ে নেমেছিলেন, সম্মিলিতভাবে লড়ে কোম্পানিকে বাধ্য করেছিলেন মাথা ঝোঁকাতে – সুযোগ বুঝে কোম্পানি একটা হাবকে বেছে নিয়ে তাদের নতুন জুলুমের খাঁড়া নামিয়ে আনল। তারা আন্দোলনকারীদের "শিক্ষা" দিতে এই জঘন্য কাজটি করল। কোম্পানি জানে যে শ্রমিকদের একতা ভেঙে দিতে পারলে, শ্রমিকদের মাথা ঝোঁকাতে বাধ্য করতে পারলে শুধু ব্লিঙ্কিট বা জোমাটো কোম্পানি নয়, সমস্ত কোম্পানির ফায়দা হবে। আর কাঁটাপুকুর হাব সহ ব্লিংকিটের সমস্ত ডেলিভারি শ্রমিকরা জানেন –যে লড়াকু একতার ফলে তাঁরা এই আংশিক জয়লাভ করতে পেরেছেন, সেই একতার জমি ভবিষ্যতে আরো শক্তিশালী হবে। যদিও কোম্পানি আজ কোনো আইনের তোয়াক্কা না করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর দুর্বার আন্দোলন না থাকার সুযোগ নিয়ে নিজেদের মর্জিমত শ্রমিকদের উপর জঘন্য আক্রমণ নামিয়ে আনছে। উল্টোদিকে ব্লিঙ্কিট, জোম্যাটো, সুইগি সহ সমস্ত অ্যাপ নির্ভর কোম্পানির শ্রমিকরাই জোট বাঁধছেন, তৈরী হচ্ছেন। দুঃখের বিষয় এটাই যে, গিগ ওয়ার্কারদের এই লড়াইয়ে সামিল হতে বা তাকে সমর্থন জানিয়ে কোন বামপন্থী দলকেই সেভাবে মাঠে নামতে দেখলাম না।
গিগ ওয়ার্কারদের সামাজিক সুরক্ষা:
সরকার বারবার করে বলে চলেছে – গিগ প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। চারটি শ্রম কোডের মধ্যে 'Social Security Act 2020' তে গিগ ওয়ার্কারদের সুরক্ষার নিদান দেওয়া আছে, যদিও তার নির্দেশনামার বাস্তব রূপরেখাই বানানো হয়নি। সামাজিক সুরক্ষার পাশাপাশি কর্মীদের অধিকারের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ। দিনে আট ঘণ্টা কাজের, স্থায়ী কাজের, মাসিক বেতনের , প্রভিডেন্ট ফান্ড আর পেনশনের দাবি এবং সফটওয়্যারে যেসব কারসাজি করে মালিকপক্ষ তাঁদের টাকা কমিয়ে দেয়, সেইসব বন্ধ করার দাবি কীভাবে তাঁরা তুলবেন? কারণ
তাঁদের সাথে তো মালিক পক্ষের মুখোমুখি আলাপ-আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে মালিক মানে তো একটি অ্যাপ। আর বর্তমান কর্মসংস্কৃতি হল – "কেউ তো তোমাকে কাজ করতে বলে নি, পোষালে কাজ কর, নাহলে বাড়ি বসে সপরিবারে না খেয়ে মর"। শিল্প সম্পর্কিত শ্রম কোড আইনটি মেয়াদি চুক্তিতে চাকরি চালু করতেই আনা হয়েছে। শ্রমিকদের চাকরির যেটুকু সুরক্ষা ছিল তাও তুলে দেওয়া হয়েছে এই আইনে। দেশে পাকাপাকি স্থায়ী চাকরি (বেসরকারি, এমনকি সরকারি ক্ষেত্রেও) বলে আর কিছু থাকবে না, স্বল্পমেয়াদের চুক্তিতে চাকরি হবে। ঐ কোড আইনে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের বা দর কষাকষির কোনও সুযোগ রাখা হয়নি। এর আগে শ্রমিকদের যেটুকু মৌলিক অধিকার কাগজে কলমে ছিল, তাও তুলে দেওয়া হয়েছে। নয়া আইনে বলা হয়েছে –ইউনিয়নের কর্মকর্তা শিল্প মালিক ঠিক করবে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের (আইএলও) যে নির্দেশিকা রয়েছে তাও এই আইনে লঙ্ঘন করা হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে, কোন কারখানা বা সংস্থায় কর্মীর সংখ্যা ৩০০ এর কম হলে সেখানে ছাঁটাই করার জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন হবে না। দেশে বর্তমানে ৮০% শিল্পে কর্মীর সংখ্যা ৩০০ জনের কম। ফলে এতে বেশিরভাগ শিল্পে ছাঁটাই অবাধ হয়ে যাবে। একেই বলে 'মালিকের পৌষমাস আর শ্রমিকের সর্বনাশ '।
প্ল্যাটফর্ম ক্যাপিটালিজম:
বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে পাঁচটি বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানির দ্বারা, যাদেরকে সংক্ষেপে GAFAM নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই শব্দের অক্ষরগুলো লক্ষ্য করুন – গুগল, অ্যামাজন, ফেসবুক, অ্যাপেল ও মাইক্রোসফ্ট। জ্ঞান -অর্থনীতি বা নলেজ ইকোনমিকে করায়ত্ত করে অ্যাপ ভিত্তিক একটা প্লাটফর্ম তৈরি করে এবং ভোক্তা ও কর্মীদের সেই নেটওয়ার্কে যুক্ত করে বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের জগত থেকে মুনাফা বের করে নিয়ে চলে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতির ধনকুবেররা। বলা বাহুল্য যে, এদের ওপর কোন রাষ্ট্রেরই কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। 'অনলাইন-শপিং' জগতের মূল সংগঠনগুলোই হল বিদেশি কোম্পানি। এইসব হর্তাকর্তারা তাদের মুনাফার একটা বড় অংশ বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছে, ফলে ওয়ার্কারদের দুর্দশা বাড়ার সাথে সাথে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর (শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, উগান্ডা, ভারত, পাকিস্তান…) অর্থনীতি ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই প্লাটফর্ম অর্থনীতির মালিকরা শ্রমিককে শ্রেণী হিসেবে কোনভাবেই সংগঠিত হতে দেবে না, তাদের 'শ্রেণী পরিচয় ' মুছে দিয়ে একক ব্যক্তি মানুষে পরিণত করতে উঠে পড়ে লেগেছে বর্তমান অর্থনীতির কর্তাব্যক্তিরা। শ্রমিকশ্রেণীর যূথবদ্ধতা, সহযোগিতা- সহমর্মিতা, আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধকে নষ্ট করে এবং একই সাথে পরিবারকে ভেঙে দেওয়ায় আগামীদিনে শ্রমিকশ্রেণী, স্থায়ী শ্রমিক –এইসব শব্দগুলো ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেবে। বরং যে দিকে এগোচ্ছে তাতে করে অদূর ভবিষ্যতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের কর্মীরাও গিগ ওয়ার্কারে পরিণত হয়ে এক দুর্বিষহ জীবনযন্ত্রণা ভোগ করবেন বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। ব্যাংক-পুঁজি ও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে ফুলে-ফেঁপে ওঠা ফিনান্স-পুঁজি উৎপাদনের জগত থেকে কোন রিয়েল ভ্যালু তৈরি করতে না পেয়ে আজ 'ফিকটিশাস ক্যাপিটালে' পরিণত হয়েছে। পুঁজির অন্ধগতিকে আজ আর সে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। ফলে একদিকে যেমন অত্যন্ত কম মজুরিতে স্বল্পকালীন চুক্তিভিত্তিক গিগ ওয়ার্কারদের জন্ম দেওয়া হচ্ছে, পাশাপাশি এই কাল্পনিক পুঁজিকে রিয়েল করার মরিয়া প্রচেষ্টায় সে তৃতীয় বিশ্বের সস্তা শ্রমকে নিংড়ে নিয়ে ছিবড়ে করছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে নির্বিচারে লুঠ করতে এই সব দেশের জল- জঙ্গল- জমি, পাহাড়-পর্বত, সবকিছুকেই নিঃশেষ করছে। ফলে দিনদিন বিপাকীয় ফাটলের রেখা দীর্ঘতর হচ্ছে এবং মানুষকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভোগবাদ- সর্বস্ব ব্যক্তিমানুষে পরিণত করা হচ্ছে। ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা, বিশ্ব মানবিকতা ও বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ পরিচয়কে। এটাই আজকের দিনে 'পুঁজির সাথে প্রকৃতির' মূল দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বকে শ্রমিকশ্রেণীর টিকে থাকা আগুয়ান অংশ ও নেতৃত্ব যত তাড়াতাড়ি আত্মস্থ করবেন এবং সেই অনুযায়ী কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করবেন, শ্রমিক-কর্মচারী তথা খেটে খাওয়া মানুষ এবং সমাজ প্রগতির পক্ষে তত মঙ্গল।
আজকে একদিকে যেমন সমস্ত ঠিকা, পরিযায়ী ও প্ল্যাটফর্ম জগতের কর্মীদের নিয়ে সংগঠিত লড়াই গড়ে তুলতে হবে, পাশাপাশি বিনষ্ট করে দেওয়া প্রকৃতি পরিবেশের মেরামতির দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের আন্তর্জাতিক লড়াইয়ের আঙিনায় মিলতে হবে কৃষক, শ্রমিক ও সমস্ত কর্মীদের। এটাই আজকের সময়ের বাস্তব দাবি।
